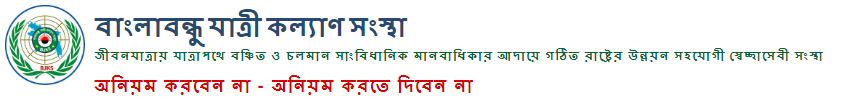বই থেকে নেয়া
১৯৭৪, সেই বছর যা আমার অস্তিত্বের শেকড় ধরে নাড়া দিয়েছিল। সেবার বাংলাদেশ ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের কবলে পড়ে।
উত্তরের প্রত্যন্ত গ্রাম ও জেলা শহরগুলো থেকে অনাহার ও মৃত্যুর খবর প্রকাশিত হতে লাগল সংবাদপত্রগুলোতে। যে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি অর্থনীতির বিভাগীয় প্রধান ছিলাম, তা ছিল দেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে। প্রথমে আমি এ ব্যাপারে বিশেষ মনোযোগ দিইনি। ক্রমেই ঢাকার রেলস্টেশন ও বাসস্ট্যান্ডগুলোতে কঙ্কালসার মানুষের দেখা মিলতে লাগল। অনতিবিলম্বে দু-চারটি মৃতদেহ পড়ে থাকার খবর আসতে লাগল। ঢাকায় বুভুক্ষু মানুষের ঢল নামল, যা শুরু হয়েছিল এক ক্ষীণধারার মতো।
সর্বত্র অনাহারি মানুষের ভিড়। এমনকি মৃত ও জীবিত মানুষের মধ্যে পার্থক্য করা কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে কোনো তফাত করা সম্ভব হয়ে উঠছিল না। বৃদ্ধদের দেখাচ্ছিল শিশুদের মতো। অন্যদিকে শিশুদের চেহারা বৃদ্ধদের মতো।
এসব মানুষকে শহরের এক জায়গায় জড়ো করে খাবার দেওয়ার উদ্দেশ্যে সরকারের পক্ষ থেকে লঙ্গরখানা খোলা হলো। কিন্তু এগুলোর সামর্থ্য ছিল প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল।
কী ভয়ংকর ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, সে ব্যাপারে সংবাদপত্রগুলো জনগণকে সতর্ক করে চলছিল। গবেষণাকেন্দ্রগুলো প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করছিল কোথা থেকে এত ক্ষুধার্ত মানুষের মিছিল আসছে? তারা জীবিত থাকলে আবার কি নিজেদের জায়গায় ফিরে যেতে পারবে? তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার সম্ভাবনা আছে?
এত সব ঘটছিল শুধু একজন দুবেলা একমুঠো খেতে পাচ্ছিল না বলে। এত প্রাচুর্যময় জগতে একজন মানুষের অন্নের অধিকার এত মহার্ঘ? চারপাশে আর সবাই যখন উদরপূর্তি করছে, তখন তাকে অভুক্ত থাকতে হচ্ছে! ছোট্ট শিশু যে এখনো বিশ্বের কোনো রহস্যেরই সন্ধান পায়নি, সে শুধু একটানা কেঁদেই চলেছেÑ শেষে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে তার প্রয়োজনীয় দুধটুকুর অভাবে। পরের দিন তার সেই কান্নার শক্তিটুকুও আর থাকল না।
অর্থনীতির তত্ত্বগুলো কীভাবে সব অর্থনৈতিক সমস্যার সহজ সমাধান করে দেয়, এই বিষয় ছাত্রদের পড়াতে পড়াতে আমি রোমাঞ্চ অনুভব করতাম। এসব তত্ত্বের সাবলীলতা ও চমৎকারিত্ব আমাকে অভিভূত করতো। এখন আমার মনে এক অদ্ভুত শূন্যতার সৃষ্টি হলো। যখন মানুষ ফুটপাতে ও ঘরের দুয়ারে অনাহারে মরে পড়ে থাকছে, তখন এসব সুচারু তত্ত্বের মূল্য কী?
অর্থনীতির এসব তত্ত্বে কঠোর বাস্তবের প্রতিফলন কোথায়? অর্থনীতির নামে আমি ছাত্রদের কী করে মনগড়া গল্প শোনাব?
এসব পাঠ্যপুস্তক, গুরুগম্ভীর তত্ত্ব থেকে আমি নিষ্কৃতি পেতে চাইলাম। বুঝলাম, শিক্ষার জগৎ থেকে আমাকে পালাতে হবে। দরিদ্র জনগণের অস্তিত্ব ঘিরে যে কঠিন বাস্তব, তা আমি আন্তরিকভাবে বুঝতে চাইলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছের গ্রাম জোবরায় জীবনমুখী অর্থনীতিকে আবিষ্কার করতে উদ্যোগী হলাম। কপাল ভালো, জোবরা গ্রাম একদম আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানা-লাগোয়া।
স্থির করলাম, আমি আবার নতুন করে ছাত্র হব এবং আমার বিশ্ববিদ্যালয় হবে জোবরা গ্রাম, গ্রামবাসী হবেন আমার শিক্ষক।
প্রতিজ্ঞা করলাম, গ্রাম সম্বন্ধে সবকিছু জানার ও শেখার ঐকান্তিক চেষ্টা করব। মনে হলো, একজন গরিব মানুষের জীবনও যদি আমি সম্পূর্ণভাবে বুঝতে পারি তো ধন্য হব। পুঁথিগত শিক্ষার বাইরে এটাই হবে আমার মুক্তি।
গ্রামবাসীর প্রত্যক্ষ কোনো সাহায্যে আসতে পারি কি না, তা দেখার জন্য আমি জোবরা গ্রামে যাতায়াত শুরু করলাম। আমার সহকর্মী অধ্যাপক লতিফী আমার সঙ্গে থাকতেন। গ্রামের প্রায় সব পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। গ্রামের মানুষজনকে অতি সহজেই আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা ছিল তাঁর সহজাত।
মুসলমানপাড়ায় নারীদের সাক্ষাৎকার নেওয়ার সময় আমাদের কথোপকথন করতে হতো চিকের আবডাল থেকে। পর্দাপ্রথা অনুসারে বিবাহিতা নারীকে বাইরের জগৎ থেকে একদম নির্বাসিতের মতো থাকতে হতো। এই নিয়ম চট্টগ্রাম জেলায় খুব কড়াভাবে পালন করা হতো। সে ক্ষেত্রে দোভাষীর মতো কাজ করার জন্য আমি আমার ছাত্রীদের ব্যবহার করতাম।
আমি চট্টগ্রামের মানুষ। স্থানীয় ভাষা আমার জানা। তাই এদের বিশ্বাস অর্জন করা কোনো বাইরের লোকের তুলনায় আমার পক্ষে সহজ হয়েছিল। তা সত্ত্বেও কাজটা খুবই কষ্টসাধ্য ছিল।
আমি বাচ্চাদের ভালোবাসি। মায়ের কাছে তাঁর সন্তানের প্রশংসা করা তাঁকে সহজ হতে দেওয়ার সবচেয়ে স্বাভাবিক উপায়।
একইভাবে সেখানে শিশুদের একটিকে কোলে তুলে নিলাম। সে কাঁদতে শুরু করল ও প্রাণপণে মায়ের কাছে দৌড় লাগল। মা তাকে কোলে তুলে নিলেন।
লতিফী জিজ্ঞাসা করলেন, ‘আপনার ছেলেমেয়ে কটি?’
জবাব এল, ‘তিনজন।’
‘চমৎকার ছেলেটি,’ আমি বললাম। আশ্বস্ত মা বাচ্চা কোলে করে দরজায় এসে দাঁড়ালেন। তাঁর বয়স কুড়ির কাছাকাছি। রোগা শরীর, ময়লা রং, চোখ দুটি গভীর ঘন কালো। পরনে তাঁর লাল একটি শাড়ি। লাখ লাখ নারী, যাঁরা অভাবের তাড়নায় উদয়াস্ত পরিশ্রম করেন, তাঁদের প্রতিনিধি মনে হলো তাঁকে।
‘আপনার নাম কী?’
‘সুফিয়া বেগম।’
আমি কোনো নোটপ্যাড বা কলম সঙ্গে নিইনি, পাছে তিনি সন্ত্রস্ত হন। পরের বার ছাত্রদের সেই ভার দিয়েছিলাম।
বাঁশের কঞ্চিগুলো দেখিয়ে বললাম, ‘এই বাঁশ কি আপনার নিজের?’
‘হ্যাঁ।’
‘কী করে এগুলো জোগাড় করলেন?’
‘কিনেছি।’
‘কত দাম নিল?’
‘পাঁচ টাকা।’
‘আপনার পাঁচ টাকা আছে?’
‘না। আমি পাইকারদের কাছ থেকে ধার করে আনি।’
‘তার সঙ্গে আপনার বন্দোবস্ত কি?’
‘দিনের শেষে মোড়াগুলো তার কাছেই বেচতে হবে দেনা শোধ করার জন্য। তারপর যা বাঁচবে তা-ই আমার লাভ।’
‘কত টাকায় একটা বেচেন?’
‘পাঁচ টাকা পঞ্চাশ পয়সা।’
‘তাহলে আপনার লাভ হলো পঞ্চাশ পয়সা।’
তিনি সম্মতি জানিয়ে মাথা নাড়লেন। তার মানে মোট লাভ হলো পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।
‘আপনি টাকা ধার করে নিজে কাঁচামাল কিনতে পারেন না?’
‘হ্যাঁ পারি। তবে মহাজন অনেক সুদ নেয়। যারা ধার নেওয়া শুরু করে, তারা আরও গরিব হয়ে যায়।’
‘মহাজন কত টাকা সুদ ধার্য করে?’
‘ঠিক নেই। কখনো শতে দশ টাকা প্রতি সপ্তাহে। আমার এক প্রতিবেশী তো প্রতিদিন শতে দশ টাকা সুদ দিচ্ছে।’
‘তাহলে এত চমৎকার মোড়া বোনার বিনিময়ে আপনার আয় এত কম? প্রতিটিতে পঞ্চাশ পয়সা মাত্র।’
‘হ্যাঁ।’
তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে সুদের হার এত সুনির্দিষ্ট ও স্বাভাবিক হয়ে গেছে যে গ্রহীতা পর্যন্ত খেয়াল করেন না এরকম চুক্তি শোষণের নামান্তর মাত্র। গ্রাম-বাংলায় ধান লাগানোর শুরুতে ধার করা এক মণ ধান ফসল কাটার সময় শোধ দিতে হয় আড়াই মণ ধান দিয়ে।
সুফিয়া বেগম আবার তাঁর কাজ শুরু করলেন। আমাদের সঙ্গে কথা বলে সময় নষ্ট করার উপায় তাঁর ছিল না। তাঁর রোদে পোড়া শীর্ণ বাদামি হাত দুটি বাঁশের চাঁচরি বুনছিল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস একইভাবে কাজ করে যান তিনি। আমি তাই দেখতে লাগলাম। এটাই তাঁর জীবনধারণের উপায়। খালি পায়ে, রুক্ষ কঠিন মাটির ওপর তিনি উবু হয়ে বসে ছিলেন। হাতের আঙুলের কড়া, নখগুলো কাদা মেখে কালো হয়ে গেছে।
তাঁর সন্তানেরা কি পারবে দারিদ্র্যের এই চক্রব্যূহ থেকে বেরিয়ে উন্নত কোনো জীবনের সন্ধান পেতে। এই নিদারুণ দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে তাঁর শিশুরা মুক্তি পাবেÑ এই চিন্তা একেবারে অর্থহীন। পেটের ভাত, মাথার ওপর ছাদ ও পরনের কাপড় জোটাতেই যখন উপার্জনে কুলোয় না, তখন কী উপায়ে তারা স্কুলে যাবে?
‘তাহলে সারা দিনের খাটুনির বিনিময়ে এই হলো আয়? পঞ্চাশ পয়সা মাত্র? আট আনা?’
‘হ্যাঁ, তাও যেদিন কপাল ভালো থাকে।’
সুফিয়া দিনে মাত্র পঞ্চাশ পয়সা রোজগার করেনÑ এই ভাবনা আমার অনুভূতিকে অসাড় করে দিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে আমরা অনায়াসে কোটি কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে কথাবার্তা বলি আর এখানে আমার চোখের সামনে জীবন-মৃত্যুর মতো সমস্যার হিসাব-নিকাশ তৈরি হচ্ছে মাত্র কটা পয়সার দ্বারা? কোথাও ভীষণ ভুল হচ্ছে। কেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষে এই নারীর বাস্তব জীবন প্রতিফলিত হয় না? নিজের ওপর ভীষণ ধিক্কার জাগল আমার। রাগ হলো গোটা পৃথিবীর ওপর, যে এ ব্যাপারে একেবারে উদাসীন। কোথাও আশার আলো নেই, সমাধানের কোনো সূত্র পর্যন্ত নেই।
সুফিয়া বেগম নিরক্ষর হলেও তাঁর কর্মদক্ষতার অভাব নেই। তিনি যে জীবিত আছেনÑ আমাদেরই সামনে বসে দ্রুত হাত চালিয়ে কাজ করছেন, শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছেন, সব রকম প্রতিকূলতা সত্ত্বেও নীরবে সংগ্রাম করে যাচ্ছেনÑ সেটাই প্রমাণ করে তিনি অন্তত একটি ক্ষমতার অধিকারী, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার অসাধারণ দক্ষতা।
মাত্র পাঁচ টাকার অভাবে কেউ এত কষ্ট সহ্য করছে, তা কখনো শুনিনি। এটা আমার কাছে অসম্ভব ও অসহনীয় মনে হলো। আমি কি সুফিয়াকে মূলধনের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ নিজের পকেট থেকে দেব? সেটা খুবই সহজ, একেবারেই জটিলতামুক্ত।
হাজার হাজার বুদ্ধিদীপ্ত অর্থনীতির অধ্যাপকেরা কেন এই গরিবদের বুঝতে চেষ্টা করেননি? সত্যিই যাদের সাহায্যের দরকার, তাদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি কেন?
সুফিয়াকে অর্থসাহায্য দেওয়ার অদম্য ইচ্ছা আমি সংবরণ করলাম। তিনি আমার দয়ার প্রত্যাশী নন। সেটা কোনো চিরস্থায়ী সমাধানও নয়।
সুফিয়ার সমস্যার কোনো সমাধান আমার জানা ছিল না। তাঁর কেন এত দুর্ভোগ, তা আমি সহজভাবে বুঝতে চেষ্টা করলাম। তিনি কষ্ট পাচ্ছেন কারণ বাঁশের দাম পাঁচ টাকা এবং তাঁর প্রয়োজনীয় নগদ টাকা নেই। তাঁর যন্ত্রণাময় জীবন একটা কঠিন চক্রের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছেÑ মহাজনের কাছে ধার নেওয়া ও তার কাছেই হাতের কাজ বিক্রি করা। এই চক্র থেকে তিনি কিছুতেই মুক্তি পাচ্ছেন না। এভাবে ভাবলে সমাধান বের করা খুবই সহজ। আমার শুধু তাঁকে পাঁচ টাকা ধার দিতে হবে।
শ্রমিক বা ক্রীতদাস মাত্র। ব্যবসাদার বা মহাজন সব সময় চেষ্টা করছে কাঁচামালের দামের সঙ্গে যৎসামান্য পারিশ্রমিক সুফিয়াকে দিতে, যাতে তিনি শুধু মৃত্যুকে রুখতে পারবেন। কিন্তু আজীবন ধার তাঁকে করে যেতেই হবে।
আমি বিবেচনা করতে শুরু করলাম, সুফিয়া যদি কাজ শুরু করার জন্য মাত্র পাঁচ টাকা হাতে না পান তো বেগার শ্রমিক হিসেবে তাঁর ভূমিকা কোনো দিনই পাল্টাবে না। ঋণই একমাত্র তাঁর সেই টাকা পাওয়ার রাস্তা। তাহলে খোলাবাজারে তাঁর তৈরি মাল বিক্রি করতে কোনো বাধা থাকবে না। কাঁচামাল ও প্রাপ্ত দামের মধ্যে গ্রহণযোগ্য লাভও থাকবে।
পরের দিন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী মাইমুনাকে ডেকে পাঠালাম। ও আমার জরিপকাজের জন্য তথ্য সংগ্রহে সাহায্য করেছিল। জোবরা গ্রামে সুফিয়ার মতো এরকম কতজন মানুষ মহাজনের কাছে ধার নিতে বাধ্য হচ্ছে, তার একটা তালিকা প্রস্তুত করতে বললাম মাইমুনাকে।
এক সপ্তাহের মধ্যে তালিকা তৈরি হলো। ৪২ জন মানুষের নাম পাওয়া গেল, যাঁরা মোট ৮৫৬ টাকা ধার করছেন।
হায় আল্লাহ, এতগুলো মানুষের জীবনে এত দুর্দশা মাত্র ৮৫৬ টাকার অভাবে!
মাইমুনা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইল। দুজনেই আমরা সেই হতভাগ্যদের চরম দুর্দশার কথা ভেবে অসম্ভব যন্ত্রণায় স্তম্ভিত হয়ে রইলাম।
ঠিক করলাম, তাঁদের আমি ৮৫৬ টাকা ধার দেব। তাঁরা আমাকে সুবিধা অনুযায়ী তা ফেরত দেবেন।
সুফিয়ার ঋণ দরকার। প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে লড়াই করার জন্য তাঁর কোনো অবলম্বন নেই। পারিবারিক কর্তব্য সাধনের জন্য, জীবিকার জন্য (মোড়া বানানো) ও চরম বিপর্যয়ের মুখে অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য তা তাঁর একান্ত দরকার।
দুর্ভাগ্যবশত গরিবদের ঋণদানের জন্য তখনো পর্যন্ত কোনো প্রথাগত প্রতিষ্ঠান ছিল না। চালু প্রতিষ্ঠানগুলোর ভ্রান্ত নীতির জন্য ঋণের বাজার পুরোপুরি মহাজনদের কবলিত হয়ে গেছে।
গরিব শুধু এ জন্য যে, তাদের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার কোনো অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর অস্তিত্ব নেই। এটা একটা সাংগঠনিক সমস্যা, কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নয়।
মাইমুনার হাতে ৮৫৬ টাকা দিয়ে আমি বললাম, ‘আমাদের তালিকার ৪২ জনকে এই টাকা ধার দিয়ে এসো, যাতে তারা মহাজনের ঋণ শোধ করতে পারে ও নিজেদের তৈরি জিনিস ভালো দামে বেচতে পারে।’
মাইমুনা জিজ্ঞেসা করল, ‘কখন তারা আপনাকে টাকা ফেরত দেবে?’
‘যখন পারবে, কোনো তাড়া নেই।’ আমি উত্তর দিলাম, ‘যখন তাদের তৈরি মাল বিক্রি করা সুবিধাজনক হবে, আমি তো আর মুনাফালোভী সুদের কারবারি নই।’ ঘটনা এভাবে মোড় নেওয়ায় মাইমুনা হতবুদ্ধি হয়ে চলে গিয়েছিল।
সাধারণত বালিশে মাথা ঠেকানো মাত্রই আমার চোখের পাতা বুজে আসে। সে রাতে আমার কিছুতেই ঘুম এল না এই লজ্জায় যে, আমি সেই সমাজেরই একজন, যে সমাজ ৪২ জন সবল, পরিশ্রমী ও দক্ষ মানুষকে তাদের জীবিকা নির্বাহের জন্য মাত্র ৮৫৬ টাকার মতো সামান্য অর্থের সংস্থান করতে পারে না।
আমি মাত্র ৮৫৬ টাকা ধার দিয়েছি। এটা ব্যক্তিগত দরদ ও ভাবাবেগপ্রসূত সমাধান মাত্র। আমি যা করেছি তা একেবারেই নগণ্যÑ এই চিন্তা তারপর কয়েক সপ্তাহ আমাকে ক্রমাগত তাড়িত করছিল। গোটা সমস্যার একটা প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান অত্যন্ত জরুরি। বিশ্বদ্যিালয়ের একজন বিভাগীয় প্রধানের পিছু ধাওয়া করার চেয়ে একজন হতদরিদ্র অভাবী মানুষের অনেক বেশি প্রয়োজন সহজতম উপায়ে মূলধনের সন্ধান পাওয়া। যতক্ষণ তা না হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত আমার চিন্তাভাবনা সাময়িক ও ভাবাবেগের পর্যায়ে থাকবে। একটা প্রতিষ্ঠান লাগবে, যার ওপর তারা নির্ভর করতে পারে।
কিছু একটা করতেই হবে। কিন্তু সেটা কী?
এ থেকেই সবকিছুর সূত্রপাত। একজন মহাজন হয়ে ওঠার কোনো বাসনাই আমার ছিল না। কাউকে ধার দিয়ে মহৎ হওয়ার ইচ্ছাও ছিল না। আমি চাইছিলাম সমস্যার আশু সমাধান। আজ অবধি আমার ও গ্রামীণ ব্যাংকের সব সহকর্মীর সেই একই স্থির লক্ষ্যÑ দারিদ্র্য সমস্যার দ্রুত নিষ্পত্তি। এই সমস্যা মানবাত্মাকে গ্লানি ও অপমান ছাড়া কিছুই দেয় না।
লেখকের আত্মজীবনী ব্যাংকার টু দ্য পুওর (ফ্রান্স, ১৯৯৭)-এর বাংলা অনুবাদ গ্রামীণ ব্যাংক ও আমার জীবন (ঢাকা, ২০০৪) থেকে সংক্ষেপিত আকারে নেওয়া।
- মুহাম্মদ ইউনূস: গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা। জন্ম ২৮ জুন, ১৯৪০, বাথুয়া, হাটহজারী, চট্টগ্রাম। ২০০৬ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী।
* সূত্র মতিউর রহমান সম্পাদিত ‘সফলদের স্বপ্নগাথা: বাংলাদেশের নায়কেরা’